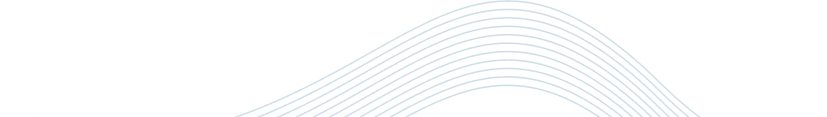বছরে ৩৭ লাখ শিশু বিনামূল্যে পাচ্ছে ১২ রোগের ১০ টিকা
সরকার সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) মাধ্যমে দেশে বর্তমানে ১২টি রোগ প্রতিরোধে ১০ ধরণের টিকা দিচ্ছে। প্রতি বছর ৩৭ লাখের বেশি শিশু নিয়মিত এসব টিকা পাচ্ছে। ১৯৮৪ সালে টিকাদানের হার ছিল মাত্র ২ শতাংশ। সেটি এখন ৮৪ শতাংশে পৌঁছেছে। তবে দুর্গম ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং মাতৃশিক্ষার অভাবের কারণে এখনো টিকার সুবিধা ও গ্রহণযোগ্যতায় বৈষম্য রয়েছে।
টিকা ব্যবস্থাপনার বৈশ্বিক জোট ‘গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন’ বা গ্যাভির সিএসও স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. নিজাম উদ্দিন আহমেদ এক প্রবন্ধে এসব তথ্য জানান। তিনি স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক।
‘বিশ্ব টিকাদান সপ্তাহ উদযাপন: বাংলাদেশে জীবন রক্ষা ও সম্প্রদায় শক্তিশালীকরণের এক অম্লান ইতিহাস’ শীর্ষক লেখায় তিনি বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচি তুলে ধরেন। আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এই সপ্তাহ চলবে।
এই বিশেষজ্ঞ জানান, বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয় ১৯৭৯ সালে পাঁচটি টিকা দেওয়া। এগুলো হলো- যক্ষ্মার বিসিজি টিকা, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস (ধনুষ্টঙ্কার) ও হুপিং কাশির ডিপিটি টিকা, পোলিও রোগের ওপিভি টিকা, টিটেনাস রোগের টিটি টিকা ও হামের টিকা। এরপর ২০০৩ সালে হেপাটাইটিস বি, ২০০৯ সালে হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধে এইচআইবি টিকা, ২০১২ সালে রুবেলা টিকা, ২০১৫ সালে নিউমোনিয়া ও মেনিনজাইটিস রোগের জন্য পিসিভি, পোলিও রোগের আইপিভি টিকা, হাম এবং রুবেলার এমআর দ্বিতীয় ডোজ টিকা এবং ২০১৭ সালের ২ অক্টোবর পোলিও রোগের এফআইপিভি টিকা দেওয়া শুরু হয়।
টিকাদান কর্মসূচিতে শিগগির আরও টিকা যুক্ত করতে যাচ্ছে বলে জানান এই বিশেষজ্ঞ। দেশ রূপান্তরের পাঠকের জন্য তার পুরো লেখাটি তুলে ধরা হলো-
‘বিশ্ব টিকাদান সপ্তাহ টিকার জীবনরক্ষাকারী ভূমিকা এবং বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অক্লান্ত প্রচেষ্টার একটি শক্তিশালী অনুস্মারক। বাংলাদেশে, টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগ (ভিপিডিএস) থেকে প্রজন্মকে সুরক্ষা দেওয়া এবং টিকাদানের সুযোগ সম্প্রসারণের অসাধারণ অগ্রযাত্রার কারণে এই উদযাপন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।
১৯৭৪ সালের মে মাসে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) চালু হয়, যার লক্ষ্য ছিল প্রতিটি শিশুকে অপরিহার্য টিকা প্রদান নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৯ সালের ৭ এপ্রিল, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে ইপিআই গ্রহণ করে। তারপর থেকে এটি দেশের অন্যতম সফল জনস্বাস্থ্য উদ্যোগে পরিণত হয়েছে।
১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ গ্লোবাল ইউনিভার্সাল চাইল্ড ইমিউনাইজেশন ইনিশিয়েটিভের আওতায় সম্পূর্ণ কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৯০ সালের মধ্যে সকল শিশুর টিকাদান নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। ১৯৮৯ সালে ঢাকা শহরসহ অন্যান্য শহরাঞ্চলে এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয় ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় টিকার সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য।
গত ৪৬ বছরে বাংলাদেশ টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৮৪ সালে যেখানে টিকাদানের হার ছিল মাত্র ২ শতাংশের নিচে, সেখানে ১৯৮৫-১৯৯০ সময়কালে কৌশলগত তীব্রতা প্রদানের মাধ্যমে ইপিআই কার্যক্রম ৪৭৬টি উপজেলা, ৯২টি পৌরসভা এবং ৬টি সিটি কর্পোরেশনে সম্প্রসারিত হয়। ১৯৯০ সালের মধ্যে সকল লক্ষ্যগোষ্ঠী, অর্থাৎ নবজাতক ও গর্ভবতী মায়েদের কাছে টিকা পৌঁছে যায়।
২০০৩ সালে ‘রিচ এভরি ডিস্ট্রিক্ট (আরইডি)’ কৌশল চালু করা হয়, যা ২০১৭ সালে ‘রিচ এভরি কমিউনিটি (আরইসি)’ কৌশলে রূপান্তরিত হয়, যার মাধ্যমে টিকা বিতরণে সমতা নিশ্চিত করার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
বাংলাদেশের টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ১৯৭৯ সালে ছয়টি প্রচলিত টিকা—বিসিজি, ডিপিটি, ওপিভি, টিটি এবং হাম—দিয়ে। এরপর থেকে টিকার তালিকা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে: হেপাটাইটিস বি (২০০৩), এইচআইবি (২০০৯ সাল), রুবেলা (২০১২ সাল), পিসিভি ও আইপিভি (২০১৫সাল), এমআর দ্বিতীয় ডোজ (২০১৫ সাল), এবং এফআইপিভি (২০১৭ সাল) যোগ করা হয়েছে। সর্বশেষ, ২০২৩ সালের ২ অক্টোবর এইচপিভি টিকা সফলভাবে চালু হয়েছে। শীঘ্রই আরও টিকা যোগ করার পরিকল্পনা চলমান রয়েছে।
জনস্বাস্থ্যের রূপান্তর ও স্বীকৃতি: এই মাইলফলকগুলো জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশে সর্বশেষ পোলিওভাইরাসের ঘটনা রেকর্ড করা হয় ২০০৬ সালে এবং ২০১৪ সালে দেশটি পোলিওমুক্ত হিসেবে ঘোষিত হয়। ২০১৮ সালে রুবেলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যও অর্জিত হয়। EPI-এর অসাধারণ সাফল্যের জন্য ২০০৯ ও ২০১২ সালে গ্যাভি কর্তৃক সেরা পারফরম্যান্স পুরস্কার প্রদান করা হয়।
প্রতি বছর বাংলাদেশে ৩৭ লক্ষেরও বেশি শিশু নিয়মিত টিকাদানের মাধ্যমে কমপক্ষে ১১টি অ্যান্টিজেন গ্রহণ করে। টিকাদানের হার টানা কয়েক বছর ধরে ৮৪ শতাংশের ওপরে স্থিতিশীল রয়েছে, যা কর্মসূচির সাফল্যের প্রমাণ। তবে, দুর্গম ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং মাতৃশিক্ষার অভাবের কারণে টিকার সুবিধা ও গ্রহণযোগ্যতায় বৈষম্য এখনও বিদ্যমান।
চ্যালেঞ্জ ও সমাধান: চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে মানবসম্পদের ঘাটতি, পর্যাপ্ত টিকার সরবরাহের অভাব, দুর্গম অঞ্চলে পরিবহন সমস্যা এবং সীমিত বাজেট বরাদ্দ। এছাড়া, ২০২৯ সালের মধ্যে গ্যাভির অর্থায়ন পর্যায়ক্রমে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশকে টিকাদান কর্মসূচির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে স্ব-অর্থায়নে রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।
ভবিষ্যতের জন্য কিছু স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপের অগ্রাধিকার আমরা দিতে পারি। যেমন- টিকাদানের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য জাতীয় সমন্বয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সেবা প্রদানের কৌশল উন্নয়ন, বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন অংশীদার ও বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ, গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ শূন্যতা পূরণ।
কিছু মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ আমাদের কে আরও বেশি সাফল্য এনে দিতে পারে। যেমন, নিয়োগ প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ, নজরদারি ও তদারকি ব্যবস্থা জোরদার, সকল স্তরে সমন্বয় উন্নয়ন।
একই সাথে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হতে হবে- ইপিআই এর জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদসহ একটি কার্যকর অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন, সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, মাইক্রোপ্ল্যানিং পরিমার্জন, টিকার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, ভিপিডিএস ও টিকা-পরবর্তী প্রতিকূল ঘটনা (এইএফআই) নজরদারি শক্তিশালীকরণ, সারাদেশে কোল্ড চেইন অবকাঠামো আধুনিকীকরণ।
বাংলাদেশের টিকাদান কর্মসূচির মূল দর্শন হচ্ছে ‘জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় রোগ প্রতিরোধ, জীবন রক্ষা এবং অর্থনীতি সুরক্ষা’ অবিচল প্রতিশ্রুতি, সমন্বিত পদক্ষেপ এবং সম্মিলিত দায়িত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ শতভাগ টিকাদান কভারেজ অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে এবং একটি টিকা-প্রতিরোধযোগ্য রোগমুক্ত দেশ হিসেবে বিশ্বে উদাহরণ স্থাপন করতে সক্ষম হবে।